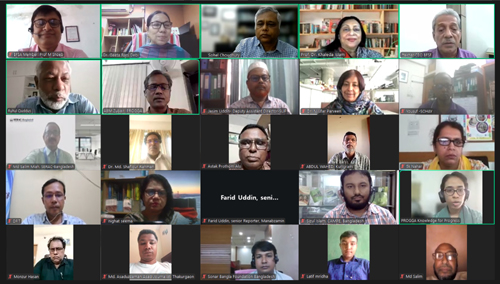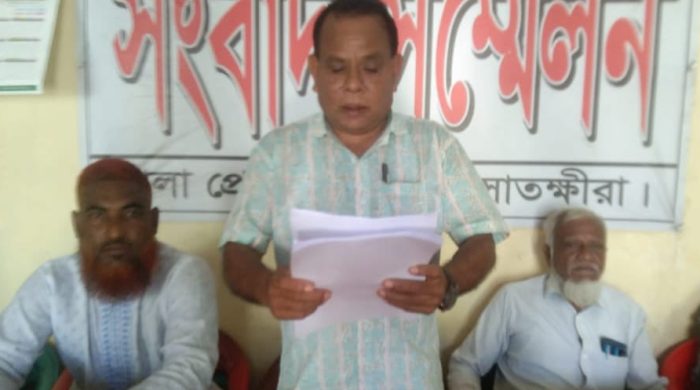আওরঙ্গজেব কামাল : ঘোলা জলের নিচে ডুবে গেছে জবাবদিহির ভাষা। সত্য তুলে আনতে গিয়ে সাংবাদিকেরা আজ পড়ছেন চাপে, হুমকিতে, এমনকি জীবনসংকটে। পেশাদার সাংবাদিকতা কি তবে দম বন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে? যদিও পেশাদার সাংবাদিকতা কখনোই ছিল না সহজ পথের যাত্রা। কিন্তু সাম্প্রতিক বছর গুলোতে এ পেশাটি যেন ঘন ঘোর অন্ধকারে হেঁটে চলেছে। তথ্য অনুসন্ধান করতে গেলে বাধা, প্রশ্ন করতে গেলেই তদবির কিংবা হুমকি—এসব যেন সাংবাদিকতার নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বহু দেশে সাংবাদিকেরা এখন রাজনৈতিক দল, কর্পোরেট গোষ্ঠী, এমনকি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকেও নিরব কিংবা প্রকাশ্য চাপের মুখে পড়ছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও মামলা অব্যাহত রয়েছে। কোনো ভাবেই থামছে না সংবাদকর্মীদের হয়রানি ও নিপীড়নের ঘটনা। এতে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসের তথ্য তুলে ধরা হয় পরিসংখ্যানে। এতে বলা হয়, ৯ মাসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ১৯ জন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও সন্ত্রাসীরা ১৪ জন সাংবাদিককে হত্যার হুমকি দিয়েছে। সংবাদ প্রকাশের জেরে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে ৬৫টি। বোমা হামলা, নির্যাতন ও হুমকি দেওয়া হয়েছে ৩৭ জনকে। আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের কর্মীদের হাতে একজন এবং বিএনপি ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের হাতে ২১ জন সাংবাদিক নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।আসকের তথ্য অনুযায়ী, জাতীয় পার্টি ও তার সমর্থিতদের হাতে দুজন, সরকারি কর্মচারীদের হাতে তিন জন হুমকির শিকার হয়েছেন। ৯ মাসে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ৯০ জন সাংবাদিক হামলার শিকার হয়েছেন। একজনকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। বৈষম্যবিরোধী আান্দোলনের নেতার হুমকির শিকার হয়েছেন একজন। আরেকজন হামলার শিকার হয়েছেন। একই আন্দোলনের পর এ সময়ে ৫২ জন সাংবাদিক মামলার আসামি হয়েছেন। অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর তিন সাংবাদিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় আরও ৬ জনসহ ৩১৫ জন সাংবাদিক হত্যা ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। একই সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ৫৩১ জন সাংবাদিক নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হন এবং হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন একজন। এতে অন্যায়, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে ওঠে, যেখানে সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক মানবতার পক্ষে শক্তি হিসেবে কাজ করেন। তারা সামাজিক অবক্ষয় এবং রাষ্ট্রীয় শোষণ-নিপীড়নের সঠিক চিত্র তুলে ধরেন। ফলে সাংবাদিকরা আজ পড়েছে বিপাকে। কখনো কখনো সাংবাদিক নিজেরাই সংবাদের শিরোনাম হয়ে যাচ্ছে।
এটি রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে গণমাধ্যম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আজ রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় ও পেশাদার সাংবাদিকদের জন্য বাংলাদেশে সাংবাদিকতা করা যেন “জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ” পরিস্থিতিতে পরিণত হয়েছে। শুধু রাজনৈতিক নয়, কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণও হয়ে উঠেছে সাংবাদিকতার বড় বাধা। বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠান বা মালিকপক্ষের স্বার্থে খবর বিকৃত করা, কিছু তথ্য এড়িয়ে যাওয়া বা পুরো রিপোর্ট ‘নিবিড়ভাবে’ সংশোধন করা আজ ‘নতুন স্বাভাবিক’ হয়ে উঠেছে। এর ফলে সাংবাদিকতা এখন আর সমাজের দর্পণ নয়, হয়ে উঠছে কর্পোরেটের মুখপাত্র। যদিও বাধা, ভয়, থ্রেট, দমন—সবকিছু সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখনো কিছু অনুসন্ধানী সাংবাদিক তাদের দায়বদ্ধতা থেকে সরে আসেননি। তারা ঝুঁকি নিয়েই তুলে আনছেন দুর্নীতি, নিপীড়ন, অবিচার কিংবা অনিয়মের খবর।ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল মিডিয়া এবং স্বাধীন অনলাইন পোর্টালগুলো হয়ে উঠছে বিকল্প কণ্ঠস্বরের মাধ্যম। তবে সেখানেও চোখ রাঙানো সেন্সরশিপ অপেক্ষা করে।বিশেষ করে অনুসন্ধানী ও ডেটা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে চরম ঝুঁকি ও আইনি জটিলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় আইন, রাজনৈতিক প্রভাব, প্রশাসনিক চাপ এবং প্রভাবশালীদের রোষানল — সব মিলিয়ে সাংবাদিকদের কাজ যেন প্রতিনিয়ত স্রোতের বিপরীতে চলার মতো। বর্তমানে বাংলাদেশে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে কমপক্ষে ২০টির বেশি আইন রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে: আদালত অবমাননা আইন, ১৯২৬,বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪,প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৭৪,তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধনী ২০১৩),বাংলাদেশ দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি,কপিরাইট আইন, অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩,তথ্য অধিকার আইন, ২০১১,নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, শ্রম আইন, ভোক্তা অধিকার আইনসহ আরও অনেক আইন।দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এসব আইনের বেশিরভাগই সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় নয়,বরং দমন ও নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর বিপরীতে সাংবাদিকদের সুরক্ষা বিধানের জন্য কার্যকর কোনো আইন নেই। আইনগত কাঠামোতে সবচেয়ে বেশি ভয়ভীতির উৎস হচ্ছে আদালত অবমাননা আইন ও মানহানি আইন। আদালত অবমাননার কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই; বিচারকের বিবেচনাতেই নির্ধারিত হয় কোন মন্তব্য অবমাননাকর হবে। অন্যদিকে, মানহানি আইন ফৌজদারি ও দেওয়ানি দুইভাবেই প্রযোজ্য। রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্বরা সাংবাদিকদের দমনে এই আইনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবাদ লিপি পাঠানোর আগেই মামলা দায়ের ও গ্রেপ্তারের নজির রয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, বেশিরভাগ আইনই উনিশ শতক কিংবা পাকিস্তান আমলের। এসব আইন আধুনিক সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও গতিশীলতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তবুও এগুলো সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হচ্ছে। উপরন্তু, সাংবাদিকদের হয়রানি করতে রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা মিথ্যা মামলা — যেমন জুলাই গণহত্যা,চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদিতেও জড়িয়ে ফেলছে। যে কারনে সাংবাদিকতা এখন হুমকীতে পড়েছে। এ পেশায় ঢুকে পড়েছে এক শ্রেনীর অশিক্ষিত পেশাদার অপরাধী ও রাজনৈতিক ব্যাক্তি বর্গ। দেশের অধিকাংশ সাংবাদিক সংগঠন গুলির দিকে তাকালে দেখাযাবে,প্রতিটি সংগঠনের প্রদানরা রয়েছেন কোন না কোন রাজনৈতিক মতআদর্শের। অনেক যায় গায় নিয়ন্ত্রন করছে রাজনৈতি ব্যাক্তি বর্গরা। তাহরে আপনারা বলুন কি ভাবে দেশে স্বাধীন সাংবাদিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে? আর দেশে স্বাধীন সাংবাদিকতা প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে কখনো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। বাংলাদেশে গণমাধ্যমের সংখ্যা কম নয়, সাংবাদিকের সংখ্যাও বিপুল, সংগঠন ও রয়েছে বহু। কিন্তু দুঃখজনক ভাবে সাংবাদিক সমাজে বিভক্তি প্রকট, যা আমাদের সবচেয়ে দুর্বল করে তুলেছে। পেশাগত দাবি আদায়, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ কিংবা আইনের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গড়ে তুলতে না পারার কারণেই সাংবাদিক নিগ্রহের হার বাড়ছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আশঙ্কা করা যায় — সাংবাদিকদের ওপর চাপ আরও বাড়বে, বাক-স্বাধীনতা আরও সংকুচিত হবে। প্রশাসন, রাজনীতি ও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে আরও বেশি সাংবাদিকের বিরুদ্ধে আইনের অপব্যবহার হতে পারে। সকলে জানে সাংবাদিকতা কোনো অপরাধ নয়, এটি একটি দায়িত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সেবা। তাই সাংবাদিকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার রক্ষায় সাংবাদিক সমাজ, সুশীল সমাজ, এবং সাধারণ নাগরিকদেরও সচেতন হতে হবে। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে একের পর এক হয়রানি, গ্রেপ্তার ও মামলা শুধু ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, এটি সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধে যদি আমরা একে অপরকে একা রেখে দিই, তাহলে একদিন আমরা কেউ-ই সত্য প্রকাশের সাহস করবো না। সাংবাদিকতা যদি হয় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ, তবে সেই স্তম্ভ আজ দুর্বল, চিড়ধরা, আর কখনো কখনো জব্দ।
সত্যকে বন্দি রাখার জন্য যত রকম অস্ত্র ব্যবহৃত হয়—হুমকি, হয়রানি, মামলা, নিয়ন্ত্রণ—তা আজ নিত্য বাস্তবতা। তবু প্রতিদিন কেউ না কেউ সাহস করে প্রশ্ন তোলে। কারণ এখনো কিছু মানুষ আছেন, যারা বিশ্বাস করেন: সত্য বলার চেয়ে বড় দায়িত্ব, আর কোনো পেশায় নেই।
লেখক:
আওরঙ্গজেব কামাল
সভাপতি, ঢাকা প্রেস ক্লাব
লেখক ও গবেষক
সাংবাদিক নিপীড়নের ঘনঘটা, সাংবাদিকতায় শ্বাসরোধ
আওরঙ্গজেব কামাল : ঘোলা জলের নিচে ডুবে গেছে জবাবদিহির ভাষা। সত্য তুলে ধরতে গিয়ে আজ সাংবাদিকেরা পড়ছেন চাপে, হুমকিতে, এমনকি জীবনসংকটে। পেশাদার সাংবাদিকতা কি তবে দম বন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে?যদিও সাংবাদিকতা কখনোই ছিল না সহজ পথের যাত্রা। তবু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই পেশাটি যেন ঘনঘোর অন্ধকারে হেঁটে চলেছে। তথ্য অনুসন্ধান করতে গেলে বাধা, প্রশ্ন করতে গেলেই তদবির কিংবা হুমকি—এসব যেন সাংবাদিকতার নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে।বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বহু দেশে সাংবাদিকেরা রাজনৈতিক দল, করপোরেট গোষ্ঠী, এমনকি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকেও নিরব কিংবা প্রকাশ্য চাপে পড়ছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও মামলা অব্যাহত রয়েছে। থামছে না সংবাদকর্মীদের হয়রানি ও নিপীড়নের ঘটনা। এতে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।
চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী:
-
১৯ জন সাংবাদিক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা নিপীড়নের শিকার হয়েছেন
-
১৪ জন সাংবাদিককে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে
-
সংবাদ প্রকাশের কারণে ৬৫টি মামলা করা হয়েছে
-
৩৭ জন হয়েছেন নির্যাতনের ও হুমকির শিকার
-
আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের কর্মীদের হাতে ১ জন, বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের হাতে ২১ জন সাংবাদিক নিপীড়নের শিকার
-
জাতীয় পার্টি ও সমর্থকদের হাতে ২ জন, সরকারি কর্মচারীদের হাতে ৩ জন হুমকির শিকার
-
দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ৯০ জন সাংবাদিক হামলার শিকার, ১ জনকে হত্যা করা হয়েছে
-
অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর ৩ সাংবাদিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে
-
সর্বমোট ৩১৫ জন সাংবাদিক ৯ মাসে হত্যা ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন
২০২৪ সালের পুরো বছরের হিসাবে দেখা গেছে, ৫৩১ জন সাংবাদিক নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং একজন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।এই পরিস্থিতি শুধু সাংবাদিক নয়, রাষ্ট্র ও সমাজের জন্যই বড় হুমকি। কারণ সাংবাদিকতা হলো অন্যায়, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার অন্যতম শক্তি।
আজকের বাস্তবতায় সাংবাদিকতা যেন হয়ে উঠেছে:
“জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ”
রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, করপোরেট নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ—সব মিলিয়ে স্বাধীন সাংবাদিকতা বাংলাদেশে মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখে। বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠান বা মালিকপক্ষের স্বার্থে খবর বিকৃত করা, তথ্য গোপন রাখা কিংবা রিপোর্ট ‘সংশোধন’ করা আজ এক প্রকার ‘নতুন স্বাভাবিক’।ফলে সাংবাদিকতা আজ আর সমাজের দর্পণ নয়, হয়ে উঠছে করপোরেটের মুখপাত্র।তবু আশার আলো রয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখনো কিছু অনুসন্ধানী সাংবাদিক রয়েছেন, যারা ঝুঁকি নিয়েও দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। দুর্নীতি, নিপীড়ন, অবিচার কিংবা অনিয়ম—তাদের প্রতিবেদনে উঠে আসছে সত্যের মুখ। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল মিডিয়া এবং স্বাধীন অনলাইন পোর্টালগুলো হয়ে উঠছে বিকল্প কণ্ঠস্বর।কিন্তু সেখানেও সেন্সরশিপের ছায়া, নজরদারি, এবং হুমকি উপস্থিত।বিশেষ করে অনুসন্ধানী ও ডেটা-ভিত্তিক সাংবাদিকতায় রয়েছে চরম ঝুঁকি ও আইনি জটিলতা। রাষ্ট্রীয় আইন, রাজনৈতিক প্রভাব, প্রশাসনিক চাপ এবং প্রভাবশালীদের রোষানলে সাংবাদিকদের কাজ যেন প্রতিনিয়ত স্রোতের বিপরীতে হাঁটা।
বাংলাদেশে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে অন্তত ২০টির বেশি আইন, যেমন:
-
আদালত অবমাননা আইন, ১৯২৬
-
বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪
-
প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৭৪
-
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধনী ২০১৩)
-
অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩
-
দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি, মানহানি আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ভোক্তা অধিকার আইন, শ্রম আইন প্রভৃতি
দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এসব আইনের বেশিরভাগই সাংবাদিকদের রক্ষায় নয়, বরং তাদের দমন ও নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হচ্ছে।বিশেষত আদালত অবমাননা ও মানহানি আইন সাংবাদিকদের সবচেয়ে বেশি ভয়ভীতির মধ্যে ফেলছে। আদালত অবমাননার কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই, বিচারকের বিবেচনার ওপর নির্ভর করে, আর মানহানি আইনও অপরাধীদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।এ ছাড়া রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা—যেমন চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণ—এইসব গুরুতর অভিযোগেও ফাঁসিয়ে দিচ্ছে।আরেকটি আশঙ্কাজনক দিক হলো, সাংবাদিকতা পেশায় ঢুকে পড়েছে এক শ্রেণির অশিক্ষিত পেশাদার অপরাধী ও রাজনৈতিক অনুগতরা। অধিকাংশ সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছে রাজনৈতিক ব্যক্তি বা মতাদর্শধারীরা। ফলে সংগঠনগুলিও অনেকাংশে বিভক্ত, একক দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দুরূহ।সংখ্যার দিক থেকে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকের ঘাটতি নেই বাংলাদেশে। কিন্তু এই বিভক্তি, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, পেশাগত সংগঠনের রাজনৈতিক মদদপুষ্ট নেতৃত্ব সাংবাদিকদের সবচেয়ে দুর্বল করে তুলেছে।এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই সাংবাদিক নিপীড়নের হার বাড়ছে।আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংবাদিকদের ওপর চাপ আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বাকস্বাধীনতা আরও সংকুচিত হতে পারে। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনের অপব্যবহার আরও জোরালোভাবে দেখা দিতে পারে।আমরা জানি, সাংবাদিকতা কোনো অপরাধ নয়—এটি একটি দায়িত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সেবা। তাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের কণ্ঠ যেন স্তব্ধ না হয়, তা নিশ্চিত করা আমাদের সবার দায়িত্ব।সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হয়রানি, গ্রেপ্তার ও মামলা শুধুই ব্যক্তি সাংবাদিকের বিরুদ্ধে নয়, এটি সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।সাংবাদিকতা যদি গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হয়, তবে সেই স্তম্ভ আজ দুর্বল, চিড়ধরা, এবং কখনো কখনো জব্দ হয়ে পড়েছে। তবু প্রতিদিন কেউ না কেউ সাহস করে প্রশ্ন তোলে, কলম চালায়, ক্যামেরা ঘোরায়। কারণ এখনো কিছু মানুষ বিশ্বাস করেন—
“সত্য বলার চেয়ে বড় দায়িত্ব আর কোনো পেশায় নেই।”
লেখক ও গবেষক:
আওরঙ্গজেব কামাল
সভাপতি, ঢাকা প্রেস ক্লাব